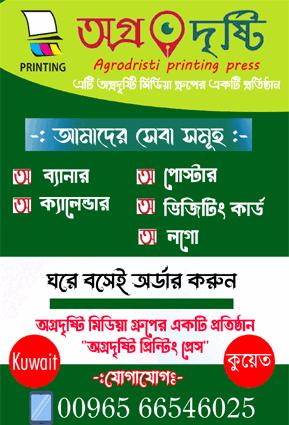বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এক অপার সম্ভাবনাময় অঞ্চল। সুপ্রাচীনকাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক অবস্থানজনিত কারণে বাংলাদেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আজ থেকে প্রায় ১৫৬ বছর আগে, ১৮৬০ সালে, ব্রিটিশ-ভারতের সরকার তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব অংশের পার্বত্য অঞ্চলকে আলাদা একটি প্রশাসনিক ইউনিট তথা একটি নতুন জেলার সৃষ্টি করে এবং নতুন জেলার নাম দেওয়া হয় ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম’। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়, তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাটি পাকিস্তান তথা পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়ে যায়। অতএব, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাও বাংলাদেশের অংশ হিসেবে অব্যাহত থাকে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দেশ যখন দ্রুত পুনর্গঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল জনগণের ঐক্যবদ্ধতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর একটি ক্ষুদ্র অংশ এই যুক্তবদ্ধতার সঙ্গে শামিল না হয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। উত্থান হয় ‘শান্তিবাহিনী’ নামক এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলের। স্বাভাবিকভাবে অবৈধ অস্ত্রধারীদের বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকার শক্তি প্রয়োগে বাধ্য হয়। ১৯৭৬ সাল থেকে শুরু হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস। ইতিহাসের সেই রক্তাক্ত পথ থেকে শান্তির পথে পার্বত্য চট্টগ্রামকে উত্তরণে বাংলাদেশের সব সরকারই সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। অবশেষে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে রক্তাক্ত অধ্যায়ের সফল অবসান ঘটিয়ে সূচিত হয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন। শান্তি চুক্তি ও বাস্তবায়ন : ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন ‘পদ্মায়’ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তৎকালীন চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি শীর্ষ নেতৃবৃন্দের পক্ষে সন্তু লারমা। এখানে উল্লেখ্য, কোনো প্রকার তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এবং কোনো বিদেশি শক্তিকে যুক্ত না করেই এ শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন হয়েছিল যা বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম। পৃথিবীর যে কোনো দেশে সাধারণত এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায়। শুরু থেকেই এই চুক্তি বাংলাদেশের বহুল আলোচিত-সমালোচিত চুক্তিগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে অবসান ঘটে তৎকালীন সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ শান্তি বাহিনীর দীর্ঘ প্রায় দুই দশকের সংগ্রামের। ফলশ্রুতিতে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও উন্নয়নের নবযাত্রার সূচনা হয়। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা হবে শান্তি ও উন্নয়নের রোল মডেল। শান্তি চুক্তির শর্তানুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে ভারত থেকে প্রত্যাগত ১২,২২৩টি পরিবারের মোট ৬৪,৬১২ জন শরণার্থীকে পুনর্বাসন করেছে। চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণরূপে এবং ১৫টি ধারা আংশিক রূপে বাস্তবায়ন করেছে। এ ছাড়াও ৯টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৩৩টি বিভাগ/বিষয়ের মধ্যে ৩০টি বিভাগ/বিষয় রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে এবং ২৮টি বিভাগ/বিষয় বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এসব বিভাগে লোকবল নিয়োগে চুক্তির শর্তানুযায়ী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সদস্যদের প্রাধান্য দেওয়ায় স্থানীয়ভাবে তাদের বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, পার্বত্য চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত একটি ব্রিগেড এবং ২৩৯টি অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। ভূমি ব্যবস্থাপনা : শান্তি চুক্তির সবচেয়ে জটিল যে বিষয়টি তা হচ্ছে ভূমি ব্যবস্থাপনা। এর জটিলতার প্রধান কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ না হওয়া। সরকার একাধিকবার পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপের উদ্যোগ নিলেও পাহাড়ি সংগঠনগুলোর বিরোধিতা, অপহরণ ও সন্ত্রাসী তত্পরতার কারণে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে ভূমি কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং সেই কমিশন কাজ করছে। ভূমি কমিশনের প্রধান ছাড়া বাকি সব সদস্যই পার্বত্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধি। বিষয়টির ব্যাপকতা এবং জটিলতার কারণেই বাস্তবায়নে একটু বেশি সময় লাগছে সমাধান করতে। শান্তি চুক্তি একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি। দুই পক্ষের জন্যই এই চুক্তিতে পালনীয় কিছু শর্ত রয়েছে। এটা ঠিক যে, শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মূল লক্ষ্য— ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রতিষ্ঠা’ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে এখনো পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী পাহাড়ি সংগঠন জেএসএসের সদস্যরা শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য তাদের পক্ষ থেকে সব শর্ত পালন করেনি এবং শুরুতেই একটি অংশ ভাগ হয়ে অস্ত্র সমর্পণে সম্মত হয়নি। পরবর্তীকালে সেই সংখ্যা আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা আরও উন্নত অস্ত্র সংগ্রহ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অসহযোগিতা অব্যাহত রাখে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাধার সৃষ্টি করে। সম্প্রতি, নিরাপত্তা বাহিনীর অপারেশনে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। পাহাড়ি শীর্ষ নেতৃবৃন্দ দাবি করে থাকেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তির দুই-তৃতীয়াংশই অবাস্তবায়িত। কিন্তু পরিসংখ্যান এই দাবি সমর্থন করে না। আমরা জানি, কিছু বাস্তবতার কারণে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হয়েছে। শান্তি চুক্তি বিষয়ে দেশের উচ্চ আদালতে একটি মামলা হাইকোর্টের রায়সহ বিচারাধীন রয়েছে। সরকারকে এসব বিষয় নিয়ে আরও দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সীমান্ত এবং সন্ত্রাসবাদ : পার্বত্য চট্টগ্রামের সঙ্গে বাংলাদেশের দুই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের অভিন্ন সীমান্ত রয়েছে এবং সেসব সীমান্তে নিজ নিজ দেশের ইমারজেন্সি অপারেশন বিদ্যমান। দুর্গমতার কারণে বাংলাদেশ আজ পর্যন্ত সেই সীমান্তের একটি বিরাট অংশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার সীমান্তে ২৬২ কিমি অরক্ষিত সীমানা রয়েছে। ফলে, সে সব অরক্ষিত দুর্গম সীমান্ত দিয়ে ওই সব দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা প্রায়শই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এতে করে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও বন্ধু দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি এবং ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। সম্প্রীতি, বান্দরবান ও রাঙামাটির কয়েকটি স্থানে বিদেশি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে যৌথ বাহিনীর গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়াও, পাহাড়ি সন্ত্রাসীদের যোগসাজশে বান্দরবান জেলা থেকে পর্যটক অপহরণসহ বিভিন্ন প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। আরও একটি উদ্বেগের বিষয় হলো সম্প্রতি সমতলের বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে পাহাড়ি সন্ত্রাসীদের অস্ত্র কেনাবেচা এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত তথ্যাদি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম থেকে জানা গেছে। এসব প্রেক্ষাপটে জাতীয় স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা ব্যবস্থার পুনঃমূল্যায়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। শান্তি চুক্তির সাফল্য : শান্তি চুক্তির ফলে পাহাড়ি শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, দলের অন্যান্য সদস্য এবং পাহাড়ের সাধারণ মানুষ যে সুবিধা ভোগ করছে তা ভুলে গেলে চলবে না। শান্তি চুক্তির পর পাহাড়ে উন্নয়ন প্রবলভাবে গতি পেয়েছে। সমতলের জেলাগুলোর মতো বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো সুবিধা গড়ে উঠেছে। সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ করে ইতিমধ্যে পাহাড়ের সব উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধীনতার আগে ১৯৭০ সালে মাত্র ৪৮ কিমি রাস্তা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য অঞ্চলে নির্মাণ করেছে প্রায় ১৫৩৫ কিমি রাস্তা, অসংখ্য ব্রিজ ও কালভার্ট। এ ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কলকারখানাসহ সম্পন্ন হয়েছে অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম। সরকারের প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ মেডিকেল কলেজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এককালের পশ্চাত্পদ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভূত উন্নতির ছোঁয়া লেগেছে। যেখানে পশ্চাত্পদ জনগোষ্ঠীর শিক্ষার মান উন্নয়নে মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ হচ্ছে সেখানেও কতিপয় স্বার্থান্বেষী নেতৃবৃন্দ বাধার সৃষ্টি করছেন। ইতিহাসে উন্নয়নকে পেছনে টেনে নিয়ে যাওয়ার এমন নজির সম্ভবত আর নেই। ১৯৭০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাত্র ছয়টি উচ্চবিদ্যালয়/কলেজ ছিল যার বর্তমান সংখ্যা ৪৭৯টি। প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন প্রায় প্রতিটি পাড়ায়। এ ছাড়াও ৫টি স্টেডিয়াম, ২৫টি হাসপাতাল এবং বর্তমানে ১৩৮২টি বিভিন্ন কটেজ ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার হার ১৯৭০ সালে মাত্র ২% শতাংশ ছিল যা বেড়ে এখন ৪৪.৬% হয়েছে। চাকমা জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার ৭৩ শতাংশে পৌঁছেছে। আমরা এ অবস্থার আরও উন্নতি দেখতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিবেশবান্ধব শিল্পকারখানা এবং পর্যটন সহায়ক শিল্প গড়ে তোলার সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। নতুন নতুন উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামকে এখন আর বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া কোনো জনপদ বলে দাবি করা যায় না। অন্যদিকে, সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উচ্চতায় ৩৫ কিমি দীর্ঘ থানচি-আলীকদম সড়ক নির্মাণ, নীলগিরি ও সাজেকের মতো উন্নত পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন আরও অনেক আকর্ষণীয় ও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এ সুবিধা আরও সম্প্রসারিত করা গেলে নেপাল এবং থাইল্যান্ডের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটন শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৪৫টি নয়নাভিরাম পর্যটন স্পট রয়েছে। সেগুলো সঠিকভাবে বিকাশ করতে পারলে প্রতিবছর ১৫-২০ হাজার কোটি টাকা উপার্জন করা সম্ভব। এতে করে রাষ্ট্র যেমন অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে তেমনি পর্যটন বিকাশের ফলে স্থানীয় পাহাড়ি জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে চাঁদাবাজি/সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অনেকাংশে কমে যাবে বলে সহজেই অনুমেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের অবস্থান : প্রথমেই একটি কথা বলা প্রয়োজন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি জনগোষ্ঠী কারও তাড়া খেয়ে, যাযাবর হয়ে বা কারও দয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে যায়নি। রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটাতেই বাঙালি কিছু পরিবারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পাহাড়ের জলবায়ু, ভূমিরূপ ও ফুড চেইন তাদের বসবাসের জন্য উপযোগী ছিল না। তা সত্ত্বেও প্রাচীনকাল থেকে সেখানে বাঙালিদের যাতায়াত ও বসবাস ছিল। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তায় ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হলে সেখানে যোগাযোগসহ বিভিন্ন সেক্টরে বিপুল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। কিন্তু পাহাড়িরা এই কাজে অভ্যস্ত বা অভিজ্ঞ ছিল না। ফলে উন্নয়ন কাজ সমাধা করার জন্য বাঙালি প্রকৌশলী, ঠিকাদার ও শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। শ্রমিকদের পক্ষে গহিন পাহাড়ি অরণ্যে কাজ করে দিনে দিনে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। ফলে নিকটবর্তী স্থানে তাদের বসতি গড়তে হয়। কোনো পাহাড়ি শ্রমিক উন্নয়নের কাজে সহায়তা করতে চাইলেও শান্তি বাহিনীর হুমকির মুখে তা পারত না। কারণ, সন্ত্রাসীরা সে সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নবিরোধী ছিল। শান্তি বাহিনী কর্তৃক নিরীহ বাঙালি হত্যা, নির্যাতন প্রক্রিয়া রোধ করতেই গুচ্ছগ্রাম সৃষ্টি করে বাঙাল ও পাহাড়িদের নিরাপত্তার আওতায় নিয়ে আসা হয়। এ প্রক্রিয়ায় বাঙালিদের জন্য ১০৯টি গুচ্ছগ্রামে ৩১ হাজার ৬২০ পরিবারের ১ লাখ ৩৬ হাজার ২৫৭ ব্যক্তিকে জায়গা-জমি দিয়ে পুনর্বাসন করা হয়। এতে বাঙালিরা নিরাপত্তা পেলেও সরকার প্রদত্ত বসতভিটা ও চাষের জমি হারাতে হয়। সেই আশির দশকের শেষভাগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাঙালিরা আর তাদের সেই ভিটা ও আবাদি জমি ফেরত পায়নি। প্রতিবছর খাজনা দিয়ে ডিসি অফিসের খাতায় জমির দখল স্বত্ব বহাল রাখলেও তাতে বসত করা, আবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ জমিতে চাষাবাদ করতে গেলেই পাহাড়ি-বাঙালি দাঙ্গা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনকি বাঙালিদের চাষকৃত জমির বিভিন্ন ফলদ ও বনজ গাছ এবং আনারস গাছ পর্যন্ত পাহাড়িরা কেটে ফেলে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের অবস্থান : পাহাড়িদের মতে, পাহাড়ের সব জমিই তাদের। বাঙালিদের ভূমিহীন করার কৌশল হিসেবে তাদের জমির খাজনা অনেক পাহাড়ি হেডম্যান গ্রহণ করে না, ডিসি অফিসে দিতে হয়। বসতবাড়ি ও ভিটার জমিতে খাজনা দিয়েও তাদের এই মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়। পাহাড়িরা সমতলে এসে বসবাস করার সুযোগ পেলেও সমতলের বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করতে পারছে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন শিল্প উদ্যোক্তার সৎ উদ্দেশ্য থাকার পরেও তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো প্রকার শিল্পায়নের প্রসার ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছেন, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। বাঙালিরা পাহাড়ে নানা বৈষম্যের অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে সরকারের দৃষ্টিগোচরে এনেছে। এরমধ্যে পাহাড়ে ব্যবসা করতে গেলে বাঙালিদের কর দিতে হয়, উপজাতিদের দিতে হয় না। উপজাতিদের ব্যাংকের সুদ ৫%, বাঙালিদের কমবেশি ১৬%। দুই লাখ টাকার নিচের ঠিকাদারি ব্যবসা একচেটিয়া পাহাড়িদের, তার উপরের কাজগুলোরও ১০% পাহাড়িদের জন্য নির্ধারিত। বাকি ৯০ ভাগ ওপেন টেন্ডারে করা হয় যাতে পাহাড়িরাও অংশগ্রহণ করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এসআই পর্যন্ত পুলিশের সব বদলি/নিয়োগ উপজাতীয় সংগঠন নিয়ন্ত্রিত। জাতীয়ভাবেও চাকরিতে ৫% কোটা তাদের জন্য নির্ধারিত। বিসিএসসহ অন্যান্য সরকারি চাকরিতেও এই কোটা রয়েছে। বাংলাদেশের খ্যাতনামা এনজিও এবং বিদেশি দূতাবাসগুলোতে চাকরির ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে অগ্রাধিকার। একজন পার্বত্য বাঙালি ছাত্র ডাবল জিপিএ-৫ পেয়েও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। অন্যদিকে জিপিএ-৫ বা তার নিচের গ্রেড পেয়ে পাহাড়ি ছেলে-মেয়েরা কোটা সুবিধার কারণে বুয়েট/মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। নানা সুবিধায় তাদের জন্য বিদেশে শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ রাষ্ট্র কর্তৃক উন্মোচিত রাখা হয়েছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন : পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার যেমন অঙ্গীকারবদ্ধ তেমনি অন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকেও অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। এ জন্য কিছু সময় ও ধৈর্য প্রয়োজন। অযথা উসকানিমূলক বক্তব্য এবং বাগাড়ম্বর হুমকি সবাইকে পরিহার করতে হবে। আশা করা যায় সব পক্ষই সেই ধৈর্য প্রদর্শন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের ধারাকে বেগবান করবে। প্রকৃতপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন কোনো একক পক্ষের দ্বারা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সরকারসহ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জাতিসত্তার সম্মিলিত ইচ্ছা ও চেষ্টার কোনো বিকল্প নেই। নেপাল এবং থাইল্যান্ডের মতো দেশে সরকার এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় নিজ নিজ দেশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে পদক্ষেপ গ্রহণ করে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ওই সব দেশে সরকারি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ চলাকালীন সময়েও সে দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পর্যটকদের অবাধ যাতায়াতে কোনোরূপ বাধার সৃষ্টি করেনি। পর্যটন শিল্পই যে উন্নয়নের চাবিকাঠি তা তারা সবাই অনুধাবন করতে পেরেছে। আমাদের দেশেও অনুরূপভাবে পর্যটন শিল্প উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অতএব, “শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নয়ন”-এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের পাশাপাশি অপার সম্ভাবনাময় পার্বত্য চট্টগ্রামে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পর্যটন শিল্পকে সরকার এবং পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত পাহাড়ি ও বাঙালি সবাইকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের আঞ্চলিক ও জাতীয় অর্থনীতিতে এই পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। এ ব্যাপারে সবাইকে অবশ্যই আন্তরিক হতে হবে। আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে, “আমি” বা “তুমি” এবং “আমরা” বা “তারা”য় বিভক্ত না হয়ে, সবাই মিলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, সেখানে বসবাসরত সব পাহাড়ি ও বাঙালি-ই এদেশের গর্বিত নাগরিক। পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের অবদান অপরিসীম ও প্রশংসার দায়ী রাখে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তথা নিরাপত্তা বাহিনী নিজ দেশেরই একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় নিয়োজিত। তারা সেখানে কোনো বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে বা যুদ্ধজয়ের জন্য নিয়োজিত নয়। তাদের লক্ষ্যই হচ্ছে শান্তি নিশ্চিত করা। পরিশেষে, পার্বত্য এলাকায় শান্তির পরিবেশ আরও সুসংহত হবে এবং সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হবে।
লেখক : সাবেক জিওসি, চট্টগ্রাম সেনানিবাস ও প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত